বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। 'কারক' শব্দটির অর্থ, যে কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এ রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু, স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে, ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।
বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ছয় প্রকারের সম্পর্ক হয়ে থাকে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক ছয় প্রকার। যেমন:
১. কর্তৃকারক,
২. কর্মকারক,
৩. করণ কারক,
৪. সম্প্রদান কারক,
৫. অপাদান কারক ও
৬. অধিকরণ কারক
নিচে একটি বাক্যের সাহায্যে এই সম্পর্কের সূত্রসমূহ দেখানো হলো:
'বাদশা নাসির উদ্দিন প্রত্যহ সকালে রাজকোষ হতে স্বহস্তে দরিদ্রদেরকে ধন দান করতেন।'
১. কে দান করতেন? বাদশা নাসির উদ্দিন (কর্তৃকারক)
২. কী দান করতেন? ধন (কর্মকারক)
৩. কী দ্বারা দান করতেন? স্বহস্তে (করণ কারক)
৪. কাদের দান করতেন? দরিদ্রদের (সম্প্রদান কারক)
৫. কোথা হতে দান করতেন? রাজকোষ হতে (অপাদান কারক)
৬. কখন দান করতেন? প্রত্যহ সকালে (অধিকরণ কারক)
১. ক্রিয়াকে 'কে' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্তৃকারক।
২. ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্মকারক।
৩. ক্রিয়াকে 'কী দ্বারা' প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে করণ কারক।
৪. ক্রিয়াকে 'কাকে' (স্বত্বত্যাগ করে প্রদান) দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে সম্প্রদান কারক ।
৫. ক্রিয়াকে 'কোথা হতে' প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অপাদান কারক।
৬. ক্রিয়াকে 'কোথায়', 'কখন' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অধিকরণ কারক।
বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে দেয়। দেখা যায়, বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলোর সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন:
সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।
এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হলো ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থগ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা' শব্দের সঙ্গে 'য়', 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়', 'এ' হলো বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোনো বর্ণ যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণমতে, সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০) বিভক্তি। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির বিন্যাস এই রকম:
সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।
সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।
এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি।
বাক্যে ব্যবহৃত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতায় সাহায্য করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়।
বাংলায় এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন:
মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।
ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।
এ জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সে জন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক-প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। ওপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। 'মাঠ মাঠ অজস্র ফসল' কিংবা 'ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নদী ভাসমান' বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে 'এ' বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে 'তে' বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। 'গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে' -এই বাক্যেও আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও 'য়' বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য করেছে। নতুবা 'গাছ পাতা রাত শিশির' কোনো বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সে জন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি-প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি-স্থানীয় কিছু শব্দ যেমন 'দ্বারা', 'দিয়ে', 'কর্তৃক', 'হতে', 'থেকে', 'চেয়ে' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
বিভক্তি দুই প্রকার। যথা:
১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি ও ২. ক্রিয়া বিভক্তি।
১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি
শব্দ বা নাম পদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি বলে। যেমন:
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ভিক্ষুক + কে)
ধাতু বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন:
তিনি বাড়ি যাবেন (যাইবেন যাইবেন/যা+বেন = যাবেন)।
শব্দ বিভক্তির সঙ্গে কারকের এবং ক্রিয়া বিভক্তির সঙ্গে কাল ও পুরুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে।
শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি কারক নির্দেশ করে বলে এগুলোকে কারক বিভক্তিও বলা হয়। কারকভেদে শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যেমন: প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।
বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে বলা হয় শূন্য (০) বিভক্তি।
একবচন ও বহুবচনে কারক বিভক্তির রূপ:
| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
| প্রথমা | শূন্য (০), অ, এ, (য়), তে | রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ |
| দ্বিতীয়া | কে, রে, এরে | দিগকে, দিগেরে, দেরে |
| তৃতীয়া | দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক | দিগের দ্বারা, দের দ্বারা, দিগ কর্তৃক |
| চতুর্থী | কে, রে, এরে | দিগকে, দিগেরে, দেরে |
| পঞ্চমী | হতে, থেকে, চেয়ে | দিগের হতে, দের হতে, দিগের চেয়ে |
| ষষ্ঠী | র, এর | দিগের, দের, গুলির, গণের |
| সপ্তমী | এ, য়, তে, এতে | দিগে, দিগেতে, গুলিতে |
পাখি ডাকে।
সে যায়।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।
উল্লিখিত বাক্য তিনটিতে ডাকে, যায় এবং খেয়েছে ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করছে যথাক্রমে পাখি, সে এবং বুলবুলি। সুতরাং পাখি, সে এবং বুলবুলি কর্তৃকারক।
যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তা বলে এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃসম্বন্ধযুক্ত পদই কর্তৃকারক।
সংজ্ঞার্থ
বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে।
কর্তৃকারকের প্রকারভেদ
ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার। যেমন:
ক. মুখ্যকর্তা: যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে-ই মুখ্যকর্তা।
যেমন:
ঘোড়া গাড়ি টানে।
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।
খ. প্রযোজক কর্তা: মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে ক্রিয়া সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা।
গ. প্রযোজ্য কর্তা: মূল কর্তার করণীয় কাজ যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন:
মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
শিক্ষক ছাত্রগণকে পড়াচ্ছেন।
এখানে 'শিশু' এবং 'ছাত্রগণ' প্রযোজ্য কর্তা।
ঘ. ব্যতিহার কর্তা: বাক্যের মধ্যে দুটি কর্তা যখন একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন:
সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।
কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি : শিহাব বই পড়ে।
দ্বিতীয়া বিভক্তি : শিমুলকে যেতে হবে।
তৃতীয়া বিভক্তি : নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।
ষষ্ঠী বিভক্তি : আমার খাওয়া হয় নি।
সপ্তমী বিভক্তি : ছাগলে কী না খায়।
ঘোড়া গাড়ি টানে। শাহেদ বই পড়ে।
সংজ্ঞা: যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।
উল্লিখিত বাক্য দুটিতে 'ঘোড়া' এবং 'শাহেদ' যথাক্রমে 'গাড়ি' এবং 'বই'-কে আশ্রয় করে 'টানা' এবং 'পড়া' ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুতরাং 'গাড়ি' এবং 'বই' কর্মকারক।
কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি: পুলিশ ডাক।
দ্বিতীয়া বিভক্তি: আমি তাকে চিনি।
ষষ্ঠী বিভক্তি: ছেলেটি বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
সপ্তমী বিভক্তি: জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
'করণ' শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায় বা উপায়। অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায়, তা-ই করণ।
সংজ্ঞা: কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। যেমন: ছেলেরা বল খেলে। বন্যায় দেশ প্লাবিত হলো। কলমটি সোনায় মোড়া।
করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি : ছেলেরা বল খেলে।
তৃতীয়া বিভক্তি: আমরা কান দ্বারা শুনি।
পঞ্চমী বিভক্তি: এ সন্তান হতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।
ষষ্ঠী বিভক্তি : তার মাথায় লাঠির আঘাত কোরো না।
সপ্তমী বিভক্তি : আকাশ মেঘে ঢাকা।
'সম্প্রদান' অর্থ স্বেচ্ছায় দান।
সংজ্ঞা: যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান করা হয়, সেই দান গ্রহীতাকে সম্প্রদান কারক বলে।
যেমন:
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। অন্ধজনে দেহ আলো। বস্ত্রহীনে বস্ত্র দাও।
কিন্তু 'স্বত্ব ত্যাগ' না বোঝালে সম্প্রদান কারক হবে না। যেমন: ধোপাকে কাপড় দাও।
এ ক্ষেত্রে 'ধোপা' সম্প্রদান কারক নয় কারণ 'ধোপাকে' কাপড় কখনোই স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া হয় না।
জ্ঞাতব্য: সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ভাষায় সম্প্রদান কারকের ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু সম্প্রদান কারক এবং কর্মকারকের বিভক্তি চিহ্ন এক। কেবল দানের প্রসঙ্গে অনেক ব্যাকরণ-বিশেষজ্ঞ সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।
সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি হয়।
সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি : গুরু দক্ষিণা দাও।
চতুর্থী বিভক্তি : দরিদ্রকে দান কর।
ষষ্ঠী বিভক্তি : ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দাও।
সপ্তমী বিভক্তি : দীনে দয়া কর।
সংজ্ঞা: যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, পতিত, গৃহীত, জাত, রক্ষিত, বিরত, দূরীভূত ও উৎপন্ন এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন:
বিচ্যুত : বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে।
পতিত : মেঘে বৃষ্টি হয়।
গৃহীত : ঝিনুক থেকে মুক্তা মেলে।
জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
রক্ষিত : বিপদে মোরে রক্ষা কর।
বিরত : পাপে বিরত হও।
দূরীভূত: দেশ থেকে বিপদ চলে গেছে।
উৎপন্ন : তিলে তৈল হয়।
ভীত : সুন্দরবনে বাঘের ভয় আছে।
অপাদান কারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তি হয়।
অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি : ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।
দ্বিতীয়া বিভক্তি : বাবাকে বড্ড ভয় পাই।
তৃতীয়া বিভক্তি : তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।
পঞ্চমী বিভক্তি : জেলেরা নদী থেকে মাছ ধরছে।
ষষ্ঠী বিভক্তি : বাঘের ভয়ে সকলে ভীত।
সপ্তমী বিভক্তি : দুধে দই হয়।
সংজ্ঞা: যে স্থানে, যে কালে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিয়ার আধার বলে। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন:
বনে বাঘ থাকে।
বসন্তে কোকিল ডাকে।
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।
প্রকারভেদ
অর্থভেদে অধিকরণ কারক চার প্রকার। যেমন:
ক. স্থানাধিকরণ;
খ. কালাধিকরণ;
গ. বিষয়াধিকরণ ও
ঘ. ভাবাধিকরণ।
ক. স্থানাধিকরণ: যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে স্থানাধিকরণ কারক বলে। যেমন: জলে কুমির থাকে।
খ. কালাধিকরণ : যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন শরতে শাপলা ফোটে।
গ. বিষয়াধিকরণ: কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অক্ষমতা প্রকাশে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে, তাকে বিষয়াধিকরণ কারক বলে। যেমন: তিনি ইংরেজিতে ভালো। শফিক গণিতে কাঁচা।
ঘ. ভাবাধিকরণ: একটি ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে নির্ভরশীল ক্রিয়াপদটি ভাববাচকে পরিণত হয়ে অধিকরণ হলে, তাকে ভাবাধিকরণ কারক বলে। যেমন: সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।
এ ক্ষেত্রে 'অন্ধকার দূরীভূত হওয়া' 'সূর্যোদয়ের' ওপর নির্ভরশীল। অতএব 'সূর্যোদয়ে' ভাবাধিকরণ কারক।
অনুরূপ: হাসিতে মুক্তা ঝরে।
অধিকরণ কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি হয়।
অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ
প্রথমা বিভক্তি : আমি আগামী কাল বাড়ি যাব।
দ্বিতীয়া বিভক্তি : মন আমার নাচেরে আজিকে।
তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান দিয়ে ঔষধটা খেয়ে নিও।
পঞ্চমী বিভক্তি : ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।
সপ্তমী বিভক্তি : বনে বাঘ থাকে।
বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ, তাকে কারক বলে। কিন্তু ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন: রামের ভাই ঢাকা যাবে।
এখানে 'রামের' সঙ্গে 'ভাইয়ের' সম্পর্ক আছে কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।
সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।
সম্বন্ধ পদের বিভক্তি
ক. সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী ('র' বা 'এর') বিভক্তি হয়। যেমন: সোনার সোনার (থালা)। তারেক + এর = তারেকের (ভাই)।
খ. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন: আজি কার আজিকার > আজকের (খবর)। পূর্বে কার পূর্বেকার (ঘটনা)।
সম্বোধন পদ
সম্বোধন অর্থ 'আহ্বান'। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন:
ওহে ইকবাল, এদিকে এসো।
মাধবী, এখানে এসো।
এখানে 'ইকবাল' ও 'মাধবী' সম্বোধন পদ। কারণ তাদেরকে আহ্বান বা সম্বোধন করে কিছু বলা হয়েছে।
সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ কিন্তু এই সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।
বিভিন্ন কারকে একই বিভক্তির প্রয়োগ
সকল কারকে 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ
কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি : সুজন স্কুলে যায়।
কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি : ঘোড়া গাড়ি টানে।
করণ কারকে 'শূন্য' বিভক্তি : ছেলেরা বল খেলে।
সম্প্রদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি : ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক।
অপাদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি : ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।
অধিকরণ কারকে 'শূন্য' বিভক্তি : আমরা খুলনা যাব।
সকল কারকে 'এ' বা 'সপ্তমী' বিভক্তির প্রয়োগ
কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি : পাগলে কী না বলে।
কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি : জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
করণ কারকে 'এ' বিভক্তি : জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।
সম্প্রদান কারকে 'এ' বিভক্তি : দীনে দয়া কর।
অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি : তিলে তৈল হয়।
অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি : বনে বাঘ থাকে।
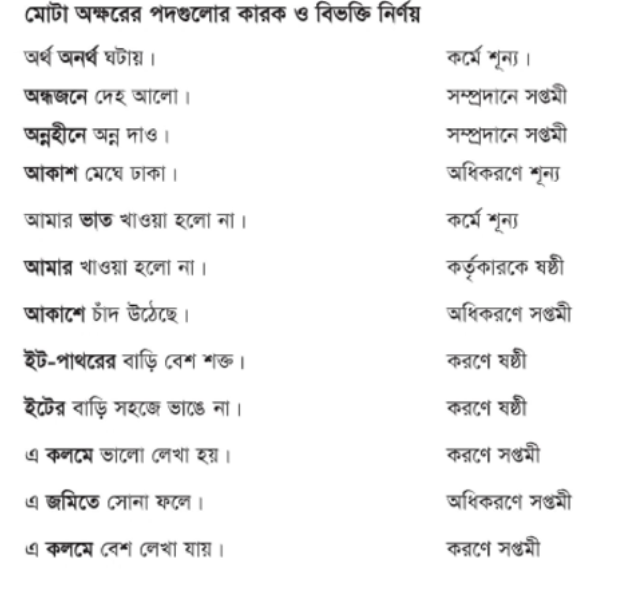



একটি শব্দকে বিভিন্ন কারকে সম্বন্ধ পদ হিসেবে এবং সম্বোধনে ব্যবহার করতে হলে বিভক্তি ও অনুসর্গ যোগ করে সংশ্লিষ্ট শব্দের যে রূপ হয়, তাকে বলা হয় শব্দরূপ। যেমন:
বালক + কে = বালককে, বালক এর বালকের।
নিচে বিশেষ্য শব্দ 'মানুষ' এবং সর্বনাম শব্দ 'আমি', 'তুমি' ও 'সে'- এর একবচনের ও বহুবচনের শব্দরূপ দেখানো হলো
(ক) বিশেষ্য শব্দের রূপ: মানুষ
| কারক | একবচন | বহুবচন |
| কর্তা | মানুষ, মানুষে (মানুষ+এ) | মানুষেরা (মানুষ + এরা) মানুষগুলি-গুলো, মানুষগণ, মানুষসকল মানুষদের। |
| কর্ম | মানুষকে (মানুষকে) | মানুষদিগকে, মানুষদেরকে (দিগ+কে) (দের+কে) |
| করণ | মানুষ দ্বারা, মানুষ দিয়া > দিয়ে মানুষকে দিয়ে | মানুষগুলো দ্বারা, মানুষগুলোকে দিয়ে |
| সম্প্রদান | মানুষকে (মানুষ + কে) | |
| অপাদান | মানুষ হইতে, মানুষ হতে, মানুষ থেকে, মানুষের কাছ থেকে | মানুষদিগ হইতে, মানুষদের কাছ থেকে; মানুষগুলোর কাছ থেকে |
| সম্বন্ধ পদ | মানুষের | মানুষদিগের, মানুষদের, মানুষগুলোর |
| অধিকরণ | মানুষের | মানুষদিগের, মানুষগণের মানুষগুলোর, মানুষদের |
| সম্বোধন | হে মানুষ! | হে মানুষগণ, মানুষসব |
(খ) সর্বনাম শব্দের রূপ: আমি, তুমি, সে
| কারক | একবচন | বহুবচন |
| কর্তা | আমি | আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে |
| কর্ম ও সম্প্রদান | আমাকে | আমাদিগকে > আমাদের, আমাদেরকে |
| করণ | আমা দ্বারা, আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া > দিয়ে | আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, আমাদেরকে দিয়ে |
| অপাদান | আমা হইতে > হতে আমার কাছ থেকে | আমাদিগ হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদের কাছ থেকে |
| সম্বন্ধ | আমার, মোর (পদ্যে) | আমাদিগের > আমাদের, মোদের (পদ্যে) আমা সবাকার (পদ্যে |
| অধিকরণ | আমাতে, আমার মধ্যে | আমাদিগেতে, আমাদিগের মধ্যে আমাদের মধ্যে |
| কারক | একবচন | বহুবচন |
| কর্তা | তুমি | তোমরা, তোমরা সব |
| কর্ম ও সম্প্রদান | তোমাকে | তোমাদিগকে, তোমাদেকে, তোমাদেরকে |
| করণ | তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়া > দিয়ে | তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগকে দিয়া, তোমাদের দিয়ে |
| অপাদান | তোমা হইতে > হতে, তোমার নিকট হইতে, তোমার কাছ থেকে | তোমাদিগ হইতে, তোমাদিগের নিকট হইতে, তোমাদের কাছ থেকে, তোমাদিগের > তোমাদের তোমা সবাকার |
| সম্বন্ধ | তোমার তব (পদ্যে) | তোমাদিগের > তোমাদের, তোমা সবাকার (পদ্যে |
| অধিকরণ | তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে | তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে তোমাদের মধ্যে |
| কারক | একবচন | বহুবচন |
| কর্তা | সে | তাহারা > তারা, তারা সব |
| কর্ম ও সম্প্রদান | তাহাকে > তাকে | তাহাদিগকে > তাদেকে, তাদেরকে |
| করণ | তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে | তাহাদিগ দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, তাদের দিয়ে |
| অপাদান | তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, তার কাছ থেকে | তাহাদিগ হইতে, তাহাদিগের নিকট হইতে |
| সম্বন্ধ | তাহার, তার, তস্য | তাদের কাছ থেকে, তাহাদিগের, তাহাদের > তাদের |
| অধিকরণ | তাহাতে, তাহার মধ্যে তাতে, তার মধ্যে | তাহাদিগেতে, তাহাদিগের মধ্যে |
'-তর' আপেক্ষিক উৎকর্ষবাচক বা অপকর্ষবাচক প্রত্যয় এবং '-তম' বহু বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একজনের সর্বাধিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষবোধক প্রত্যয়।
দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণের সঙ্গে '-তর' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং দুয়ের বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় '-তম' প্রত্যয়। মোটকথা, সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী দুয়ের মধ্যে তুলনা করতে হলে বিশেষণের সঙ্গে '-তর' এবং বহুর সঙ্গে তুলনা করতে হলে '-তম' যোগ হয়।
'তর' এবং 'তম' এ দুটি প্রত্যয়কে একত্র করে হয়েছে 'তরতম, যার অর্থ 'কম-বেশি'।
লক্ষণীয় 'তারতম্য' শব্দটিও 'তরতম' থেকে তৈরি। যেমন তরতম য = তারতম্য।
'তর' এবং 'তম'-এর প্রয়োগ
| মূল বিশেষণ শব্দ | তর-যোগে | তম-যোগ |
| বৃহৎ | বৃহত্তর | বৃহত্তম |
| মহৎ | মহত্তর | মহত্তম |
| দীর্ঘ | দীর্ঘতর | দীর্ঘতম |
| প্রশস্ত | প্রশস্ততর | প্রশস্ততম |
'-তর' '-তম'-এর বাক্যে প্রয়োগ
১. চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
২. হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত।
৩. কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত।
৪. মালদ্বীপ বাংলাদেশের চেয়ে ক্ষুদ্রতর।
৫. মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।
বিশেষণের তারতম্য
কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ গুণ, অবস্থা ইত্যাদি তুলনা করা যায়। এভাবে তুলনায় ভালো-মন্দ, কম-বেশি বা উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়ে থাকে। এ ধরনের তুলনা করাকে বিশেষণের তারতম্য বলে। বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত দুটি রীতি আছে।
বাংলা রীতি
(ক) দুইয়ের মধ্যে তুলনায়, যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তার পরে 'অপেক্ষা', 'চেয়ে' প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন: চাটগাঁর চেয়ে ঢাকা বড় শহর। রূপা অপেক্ষা সোনা দামি ইত্যাদি।
(খ) বহুর মধ্যে তুলনায় একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানতে হলে 'সর্বাপেক্ষা', 'সবচেয়ে', 'সকলের চেয়ে' ইত্যাদি পদ বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। যেমন: এ ছাত্রটি সবচেয়ে ভালো। সে সকলের চেয়ে ভালো লেখে ইত্যাদি ।
সংস্কৃত রীতি
(ক) দুইয়ের মাঝে তুলনায় বিশেষণ শব্দের শেষে 'তর' প্রত্যয় এবং দুইয়ের বেশির মাঝে তুলনায় 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: বাঘ অপেক্ষা হাতি বৃহত্তর। গাঁয়ে তিনিই বিজ্ঞতম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:
| মূল বিশেষণের শব্দ | তর-যোগে | তম-যোগে |
| দীর্ঘ | দীর্ঘতর | দীর্ঘতম |
| মহৎ | মহত্তর | মহত্তম |
| বৃহৎ | বৃহত্তর | বৃহত্তম |
| প্রশস্ত | প্রশস্ততর | প্রশস্ততম |
(খ) 'তারতম্য' বোঝাতে সংস্কৃত ঈয়স্ (দুইয়ের মধ্যে) ও ইষ্ঠ (বহুর মধ্যে) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন:
| মূল বিশেষণের শব্দ | ঈয়স্-যোগে | ইষ্ঠ-যোগে |
| গুরু | গরীয়স্ > গরীয়ান | গরিষ্ঠ |
| বৃদ্ধ | বর্ষীয়স্ > বর্ষীয়ান | জ্যেষ্ঠ |
| বলবৎ | বলীয়স্ > বলীয়ান | বলিষ্ঠ |
বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত রীতি খাঁটি বাংলাতেও প্রচলিত। তবে বাংলা ভাষার কিছু নিজস্ব রীতিও আছে। দুয়ের মধ্যে তুলনায় চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন:
জেমসের চেয়ে যোসেফ বেশি বলবান। রাম অপেক্ষা শ্যাম বুদ্ধিমান।
বহুর সঙ্গে তুলনায় 'সর্বাপেক্ষা', 'সবচেয়ে', 'সবচাইতে', 'সকলের মধ্যে', 'সবার চাইতে' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।
যেমন: পশুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গাছের মধ্যে বটগাছ সবচেয়ে বিশাল। সবচাইতে ভালো খেজুর রস আর শীতের পিঠা।
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)
১। নিচের কোন বাক্যে দ্বিতীয় বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে?
ক. শিমুকে যেতে হবে
খ. সজল গান গায়
গ. দেশের সেবা কর
ঘ. রাজায় রাজায় যুদ্ধ
২। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। কোন কারকের উদাহরণ?
ক. কর্তৃ কারক
খ. কর্ম কারক
গ. করণ কারক
ঘ. সম্প্রদান কারক
৩। বনে বাঘ থাকে। নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকের ৭মী বিভক্তির উদাহরণ?
ক. কর্তৃ
খ. অধিকরণ
গ. অপাদান
ঘ. কর্ম
common.read_more